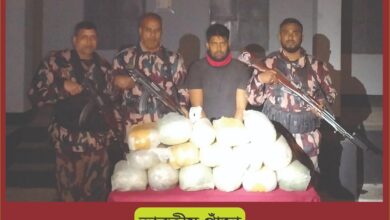কলকাতায় বসে দুই বাংলার নদী-মানুষদের কথা বললেন সুমনা

টাইমস ২৪ ডটনেট:নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল বহু প্রাচীনকাল থেকেই। আর সেই থেকেই শুরু নদীর সঙ্গে জীবনের তুলনা। নদীর গতি সর্বদাই আমাদের অনুপ্রাণিত করে। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস লেখার প্রয়াস বহু ঔপন্যাসিকই করেছেন। নদী, নদীকেন্দ্রিক জীবিকা, মাঝি-মাল্লা তাদের পরিবার ও সমাজ এবং বিকল্প আয়ের নানা অনুসন্ধানের চিত্র এইসব যেমন নানা রচনায় আছে তেমনি অন্ত্যজ সমাজের নানা সংঘাত কিম্বা শ্রমজীবী মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবনের বিচিত্র চিত্র স্থান পেয়েছে এইসব রচনায়। নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনের নানা পরিবর্তনকে ঔপন্যাসিকগণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমুদ্রকেন্দ্রিক বিখ্যাত উপন্যাস Ernest Hemingway-এর The Old Man and the Sea’-এর মতোই গঙ্গা, পদ্মা, তিতাস, কোপাই, তিস্তা প্রবহমান হয়ে জীবনকে প্রতিফলিত করেছেন রচনাকারদের জীবন দশর্নের তারতম্যে। এই সমস্ত নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস নিয়ে চমৎকারভাবে সূত্রে গেঁথেছেন ড. সুমনা পাত্র তাঁর নতুন ‘বাংলা উপন্যাস: নদীজীবনের বহুমুখী পাঠ’ গ্রন্থ’টিতে।
একটা কথা বলতেই হবে, কাঁটাতারের বিভাজনকে সরিয়ে দুই বাংলার সাহিত্যকে একত্রিত করলে দেখা যায় বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। নদীকেন্দ্রিক রোমান্টিসিজম কোনও দেশকালের সীমারেখা মানে না। নদীনির্ভর জীবিকা অর্জনকারীরা প্রায়শই জীবিকার প্রয়োজনে সমুদ্র যাত্রা করেন। সমুদ্রের বুকে ভাসমান জেলে-নাবিকদের সঙ্গে নদীনির্ভর জেলে-মাঝিদের জীবন-জীবিকার সাদৃশ্য চোখে পড়ে বারবার। তাই বাংলা সাহিত্য পাঠকদের কাছে জলজীবন সর্বোপরি জলজীবীদের কথা বরাবরই আকর্ষণের বিষয়।
নদীকেন্দ্রিক বাংলার প্রান্তিক মানুষদের কাছে নদী সাক্ষাৎ মাতৃস্বরূপা। ভয়াল বন্যার আতঙ্ককে ভুলিয়ে রেখে নদী তাদের জোগায় সোনালী ফসল। সে এমনই এক জীবনধারণের মাধ্যম যেখানে বিপদকে অগ্রাহ্য করতে হয় প্রতিনিয়ত। সাংসারিক জোয়ালের তাড়নায় ভয় ও ক্লান্তির বিড়ম্বনা ভুলে ভাটিয়ালি ও সারি গানের সুরে একদল প্রান্তিক মানুষ এগিয়ে চলে শক্ত হাতে হাল ধরে। নদীর বুকে তাদের সঁপে দিয়ে ঘরণীরাও সাহসে ভর করে দিন কাটায়।
দুই বাংলার সাহিত্যকে যেমন নদী বারবার সমৃদ্ধ করেছে, ঠিক তেমনই সুমনার নদী-মানুষ সংক্রান্ত বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর নদীর প্রতি ভালোবাসা। দুই বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ)-এর প্রতি আকর্ষণ। আন্দরের টান। লেখিতা তাই তো বলেছেন, “শুধু গঙ্গা নয়, পরপর দু’বার রাজশাহী যাওয়ার সুবাদে পদ্মাও আমার নিতান্ত পরিচিত”।
তাই তো কেবলমাত্র আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে নয়, বৃত্তিজীবী শ্রেণির জীবনকথা হিসেবেই দুই বাংলার নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় উঠে এসেছে। আলোচনার অনুষঙ্গেই নদীনির্ভর বৃত্তিধারী মানুষদের জীবন-জীবিকা, তাদের সামাজিক অবস্থান, তাদের পারিবারিক জীবন, তাদের সাংগীতিক জগৎ, সর্বোপরি তাদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম যে বৈচিত্রময় ভাষা, তার কথাও উঠে এসেছে। আর বিষয়ের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, প্রয়োজনে তুলনামূলক বিচারে এই শ্রেণির উপন্যাসের মূল চরিত্র ও বাস্তবতাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখিকা।
আর এখানেই সাফল্য বইটির। আশা করা যায় শুধু বাঙলা ভাষার পাঠকরাই নন, আগামী দিনের দুই বাংলার নদী নিয়ে কাজ করা প্রতিটি মানুষ, ভারত-বাংলাদেশের নদীজীবী মানুষদের কথা তুলে ধরবেন যারা তাঁরা– সকলেই বইটি থেকে কোনও না কোনও ভাবে উপকৃত হবেন।